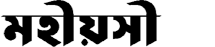আবু এন. এম. ওয়াহিদ
সেদিন আমার স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলাম এক নেফ্রোলজিস্টের (কিডনি বিশেষজ্ঞ) কাছে। ঢুকেই ডাক্তারের অফিসের ফ্রন্টডেস্কে রিপোর্ট করে ওয়েটিংরুমে বসে আছি। কিছুই করার নেই তাই হাতের কাছে পেয়ে এক পুরনো ম্যাগাজিনে চোখ বুলাচ্ছি। এমন সময় দরজায় আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি দু’জন রোগী এসে ঢুকছেন। দেখতে যদিও দু’জনকেই রোগী মনে হচ্ছিল তথাপি আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে নেফ্রোলজিস্টের কাছে রোগী এসেছেন একজনই এবং অন্যজন নিছক সঙ্গ দিচ্ছেন। ডাক্তারের অফিসে অহরহই তো কত সুখী-অসুখী মানুষ আসা যাওয়া করে, কিন্তু ওই দিন এ দু’জনের প্রতি আমার বিশেষ নজর পড়ল কেন? কারণ অবশ্য একটি আছে, আর এ নিয়েই আজকের এই ছোট্ট নিবন্ধ।
যাঁদের কথা বলছি তাঁরা দুজনই বৃদ্ধ। বয়স আনুমানিক আশির বেশি বৈ কম হবে না। একজন পুরুষ আরেকজন মহিলা। কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম, তারা দুজন স্বামী-স্ত্রী। কিভাবে বুঝলাম সেটা একটু পরেই পাঠকদের কাছে খোলাসা হয়ে যাবে। ভদ্রমহিলা বয়সের ভারে অথবা অগ্রসরমান জটিল কিডনি রোগে একেবারে কাবু হয়ে গেছেন, হাঁটতে পারছেন না। অনেক কষ্টে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলছেন, তাও আবার চার চাকার ওয়াকারের ওপর ভর করে। ভদ্রলোক একহাতে স্ত্রীকে ধরেছেন এবং আরেক হাতে লাঠির সাহায্যে এক পা এক পা করে এগোচ্ছেন এবং হাঁফাচ্ছেন। এভাবে অতি কষ্টে তারা দুজন এসে ঢুকলেন ডাক্তারের ক্লিনিকে। ক্লান্ত হয়ে এসে দুজনই চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়লেন। তাঁদের দেখে ভীষণ করুণা হল, মায়া হল, ভাবলাম, ‘দু’জনই তো রোগী, কে কাকে দেখে’!
পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে ফ্রন্টডেস্কে কর্তব্যরত ডাক্তারের নার্স মিসেস লিলি বলে ইনসুরেন্সের কাগজপত্র নিয়ে হাজির হতে ডাক দিলেন রোগিনীকে। পেসেন্ট ডাক শুনতে পেলেন কীনা বুঝলাম না, ইত্যবসরে ভদ্রলোক পড়িমরি করে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন এবং দু’কদম সামনে এগিয়ে গিয়ে বলিষ্ঠ কন্ঠে বললেন, ‘আই অ্যাম মিস্টার লিলি’। অর্থাত তাঁর স্ত্রীর হয়ে তিনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বের করে দিয়ে দর্শনার্থী রোগীদের হাজিরা খাতায় মিসেস লিলির নাম লিখে আবার গিয়ে চেয়ারে বসলেন তাঁর সহধর্মিনীর পাশে। যেভাবে তাঁরা দুজন গাড়ি থেকে নেমে লিফ্টে চড়ে তিনতালায় উঠে ওয়াকার ও লাঠির ওপর ভর করে ডাক্তারের অফিসে এসে ঢুকলেন, তা মারাত্মক রকম ঝুঁকিপূর্ণ বৈকি। নিরুপায় হয়ে জেনেশুনেই তাঁরা এভাবে আসতে যে বাধ্য হয়েছেন সেটা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এই চলার পথে যে কোনো মুহূর্তে পড়ে গিয়ে তাঁদের একজনের কিংবা দু’জনেরই হাত পা ভেঙ্গে যেতে পারত। এ অবস্থায় নিজের ছেলেমেয়ে, অথবা আরো অল্প বয়সী আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কিংবা প্রতিবেশী কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসা উচিত ছিল। হাতের কাছে কাউকে পাননি নিশ্চয়ই। জীবনটা বড়ই কঠিন, ‘জগতে কে কাহার’? বস্তুবাদি পাশ্চাত্য সমাজের এটা একটা ভীষণ খারাপ দিক। বৃদ্ধ বয়সে মানুষের দেখাশোনা ইউরোপ আমেরিকায় একটি বিশাল পারিবারিক, সামাজিক, এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যা হয়ে আছে। এবং এটা আজ নতুন নয়, অনেক দিন ধরেই চলছে এভাবে। আজকাল বাংলাদেশেও এ সমস্যা দিনে দিনে প্রকট আকার ধারণ করছে।
মিস্টার ও মিসেস লিলির দূরবস্থা দেখে মনে মনে ভাবলাম, “এ দু’জন লিলির জীবনই শুধু এমন বিষাদময় নয়। আরো অনেক লোক, এমন কী আমার জানামত নিজের ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেও এমন বৃদ্ধ নারী-পুরুষ অনেক আছেন যাঁদের নিত্য দিন এভাবে অসহায়ের মতই কাটছে, অর্থাত ‘কে কাকে দেখে’! দুঃসময়ে প্রিয়জনরা থেকেও কাছে থাকে না বা থাকতে পারে না। অন্যের কথাইবা বলি কী করে, মাত্র বছর খানেক হল আমার শ্বশুর মারা গেছেন তাঁকে শেষ সময়ে দেখার জন্য না পেরেছি আমি যেতে না আমার স্ত্রী। কিছুটা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াজনিত পেরেশানির কারণে কিছুটা গাফলতির জন্য। এ জন্য আমার আফসোস হয় আর আমার স্ত্রীর তো দুঃখের সীমা নেই। অবশ্য আমার শাশুড়ির শেষ সময়ে আমার স্ত্রী তাঁর পাশে ছিল। প্রায় ৩০ বছর আগে আমার বাবা মারা গেছেন। সে সময় নিজে ছাত্র ছিলাম বাবাকে দেখতে যেতে পারিনি। মার মৃত্যুতেও তাঁর পাশে থাকা হয়নি বলে আজও আমার প্রাণ কাঁদে।
এ তো যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের কথা। কিন্তু তাঁরা যখন বেঁচেছিলেন, তখনও বা আমরা কী করতে পেরেছি। ওই বয়সে সন্তান হিসেবে তাঁদের প্রতিও আমাদের দায়িত্বটি সঠিকভাবে পালন করতে পারিনি। তাঁরা ছিলেন একদেশে আমরা আরেক দেশে। যখন তখন দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ সুযোগ ছিল না। টেলিফোনে কথা হত কেবল শাশুড়ির সঙ্গে, মার সাথে হত না কারণ তিনি ছিলেন অলজাইমার রোগী -জবান বন্ধ। কাউকে চিনতেও পারতেন না। শেষের দিকে কয়েক বছর নিজের সন্তানদেরকেও ঠাহর করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি ২৪ ঘন্টাই বিছানা বন্দি থাকতেন। সে তুলনায় বয়স আন্দাজ আমার শাশুড়ি অনেক ভাল ছিলেন। মারা যাওয়ার কয়েক দিন আগ পর্যন্ত তিনি স্বাভাবিক জীবন যাপন করে গেছেন। বৈষয়িক দিক থেকে তাঁদের কারোরই অসুবিধা ছিল না, তবুও বয়সকালে মা-বাবা তো তাঁর সন্তানদেরকে দেখতে চাইতেন, কিন্তু পারতেন না। তাঁদের এমন আশা তো আমরা পুরণ করতে পারিনি। এটাই বা কম কম দুঃখের কী! নিজেরা যখন বৃদ্ধ পিতা-মাতার দেখাশোনা করতে পারিনি, আমরা যখন বুড়ো হব তখন কীভাবে নিজেদের সন্তানদের কাছে দাবি করব আমাদের কাছে থাকার জন্য বা তাদের কাছে আমাদের রাখার জন্য। ডাক্তারের অফিসে বসে এলোপাথাড়ি এ সব কথা ভাবতে ভাবতে মনটা খুব খারাপ হয়ে আসল, মুহূর্তে অনুভব করলাম চোখের কোণগুলো ভিজে আসছে।
দেহের চোখ মুছে মুছে মনের চোখে পেছন ফিরে তাকালাম। মনে পড়ল অনেক দিন আগের কথা। আমি তখন কানাডার ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পিএইচডির ছাত্র। সে সময় ওই ইউনিভার্সিটির ইকোনোমিক্স ডিপার্টমেন্টে প্রতি শ্রক্রবার বিকেলে বিভাগীয় সেমিনার হত। সেমিনারে একেক দিন একেকজন প্রফেসার একেকটি বিষয়ের ওপর তাঁদের গবেষণা সমৃদ্ধ প্রবন্ধ উপস্থাপন করতেন। মাঝেমধ্যে বাইরে থেকেও সেমিনার উপলক্ষে ভিজিটিং প্রফেসাররা আসতেন। সেমিনারে উপস্থাপকরা তাঁদের গবেষণার ফলাফল জানাতেন এবং এসব নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হত, গভীর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হত, উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক হত। ওইসব সেমিনারে গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টস হিসেবে আমাদেরও থাকতে দেওয়া হত। দেওয়া হত বললে একটু কমই বলা হয়, বরং আমাদের সেমিনারে উপস্থিত থাকার জন্য রীতিমত উতৎসাহীত করা হত। ওইসব সেমিনারে আমি বিশেষ কিছু বুঝতাম না। তবে প্রফেসারদের চিন্তার প্রসারতা, বুদ্ধির প্রখরতা, এবং জ্ঞানের গভীরতা দেখে দারুণভাবে মুগ্ধ হতাম। আর ভাবতাম, বাংলাদেশে এমন গভীর, নিবিড়, এবং নির্ভেজাল জ্ঞানের চর্চা কবে হবে!
নেফ্রোলজিস্টের অফিসে বসেই ওই সব সেমিনারের এক বিশেষ দিনের কথা মনে পড়ল। একদিনের সেমিনারের মূল প্রবন্ধ ও তাঁর ওপর আলোচনা-সমালোচনা শেষে একটি দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ সাইড টক বা সাইড ডিসকাশন হয়েছিল। এতেও বেশ উত্তেজনাপূর্ণ তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। সাইড টকের বিষয়বস্তু ছিল সিনিয়র সিটিজেনস অর্থাৎ ‘বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতার দেখাশোনার দায়িত্ব’। এটা কী সন্তানের, সমাজের, না রাষ্ট্রের, এবং কীভাবে কার্যকরভাবে কম খরচে এ গুরুদায়িত্ব পালন কার যায়, তা নিয়ে প্রফেসারদের মধ্যে চলছিল তুমূল বিতর্ক।
ওই সময় কানাডার অর্থনীতির সবচেয়ে রমরমা খাত ছিল সিনিয়র সিটিজেনস হোমস। অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ লোকজনদের দেখাশোনার জন্য তখন সারা দেশে নির্মিত হচ্ছিল সিনিয়র সিটিজেনস রেসিডেন্স। এতে ফেডারেল এবং প্রাদেশিক সরকারের ভর্তুকিও ছিল বেশ। ফলে সরকারের উভয় স্তরে দেখা যাচ্ছিল রাজস্ব ঘাটতি। কীভাবে সরকারের এ খরচ কমানো যায় তা নিয়ে চলছিল আলোচনা ও যুক্তি-তর্ক। অন্যান্য দেশের তুলনায় কানাডায় এ সমস্যা একটু বড় এবং জটিল ছিল। কারণ ওই দেশের মানুষের গড় আয়ু পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বেশি ছিল। সেদেশের মানুষ অনেক দিনে বাঁচে। তাই রিটায়ার করার পর বৃদ্ধ বয়সে বিশেষ করে অসুস্থ পিতামাতার দেখাশোনা কানাডার জন্য এক বিরাট সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই বিতর্কের খুঁটিনাটি সব কথা সেদিন বুঝিনি, এবং যেটুকু বুঝেছিলাম তারও তেমন কিছু মনে নেই। তবে অবশেষে সবাই যে উপসংহারে একমত হয়ে বিতর্কের অবসান টেনেছিলেন তা পরিস্কাভাবেই মনে আছে। কথাটি ছিল, “ইন ওল্ড এজ, নাথিং লাইক ওবিডিয়েন্ট চিল্ড্রেন”। অর্থাত, ‘বৃদ্ধ বয়সে, সুসন্তানের তুলনা নেই’। কথাটা আমি একটু অন্যভাবে বলতে চাই। আমাদের জীবনের সব ব্যাপারে আল্লাহ্ই চূড়ান্ত ভরসা, বৃদ্ধ বয়সে সুসন্তানের বড়ই প্রয়োজন। এ কথা শুধু ইউরোপ, আমেরিকা, এবং কানাডাই নয়, সারা পৃথিবীর বেলাই প্রযোজ্য।
পরিশেষে এ প্রসঙ্গে প্রতিটি পিতামাতাকে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে দু’টো বিষয় খেয়াল রাখতে বলব। প্রথমতঃ তাদেরকে সুশিক্ষা দিয়ে প্রতিযোগিতাশীল বৈষয়িক দুনিয়ার জন্য সুযোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সন্তানদেরকে আদব কায়দা এবং নৈতিক শিক্ষা এমনভাবে দিতে হবে যাতে তারা জজ ব্যারিস্টার, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সাথে পিতামাতার প্রতি সহানুভূতিশীল আদর্শ সুসন্তান হয়ে বড় হয়। আর এ ক্ষেত্রে ধর্ম (সে যে ধর্মই হোক না কেন) নিঃসন্ধেহে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বলা যত সহজ, সঠিকভাবে কাজটি করা ততই কঠিন। এ দুনিয়ায় দিনের শেষে আমরা কে কতখানি সফল তা নির্ভর করে ছেলেমেয়েদের আমরা কীভাবে মানুষ করতে পেরেছি তার ওপর। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, ‘অ্যা ট্রি ইজ নউন বাই দি ফ্রুট ইট বেয়ারস্’ অর্থাত্, ‘ফলেই বৃক্ষের পরিচয়’। সুসন্তান মানুষ হয়ে শুধু মা-বাবার মুখই উজ্জ্বল করে না বরং বিপদে-আপদে তাঁদের সাহায্যও করে।
লেখকঃ ড. আবু এন. এম. ওয়াহিদ; অধ্যাপক – টেনেসী স্টেইট ইউনিভার্সিটি;
এডিটর – জার্নাল অফ ডেভোলাপিং এরিয়াজ