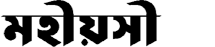আবু এন এম ওয়াহিদ
আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ, আপ্যায়ন, দাওয়াত, ইত্যাদি শব্দের সাথে আপনারা অবশ্যই পরিচিত আছেন। আপনারা এ-ও জানেন, দৈনন্দিন ব্যবহারে এ সবের প্রতিশব্দ আরও আছে। যেমন চট্টগ্রামে গেলে শুনতে পাবেন, ‘মেজবানি’। এখন হয় কি না জানি না, তবে আমার ছেলেবেলায়, একই অর্থে ভিন্ন আরও দু’টো শব্দ সিলেটের গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত হতো, যেমন – ‘জিয়াফত’ এবং ‘তামদারি’। গেল শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশকে আমাদের বাড়িতেই এগুলো চালু ছিল, অবশ্য কেবল দাদীর মুখেই শুনতাম। বাকি সবাই মিলে আমরা ‘দাওয়াত’কে দাওয়াত-ই বলতাম। আজ দাদী নেই, নিশ্চয়ই ওই বাড়ির আকাশে বাতাসে সে ধরনের সেকেলে গেঁয়ো শব্দ আর ঢেউ তুলে না। এক দিন আগেও আমার ধারণা ছিল, ‘মেজবানি’, ‘জিয়াফত’ এবং ‘তামদারি’ একান্তই আঞ্চলিক শব্দমালা, শুদ্ধ বাংলায় এ সবের কোনও জায়গা নেই। আজ অভিধানের পাতা উল্টাতে গিয়ে বিস্ময়ের সাথে আবিষ্কার করলাম, আমার ধারণা ভুল! আমরা এখন বলি আর না বলি, যে করেই হোক, পুরনো এই শব্দগুলো সসম্মানে বাংলা ভাষায় স্থায়ী আসন গেড়ে বসে আছে! মাতৃভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর উৎপত্তি, বিবর্তন, অর্থ ও ব্যবহার নিয়ে আমার কৌতূহলের কোনও কমতি নেই, কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধির অভাবে এই আলোচনা সে দিকে আরও এগিয়ে নেওয়ার মতন তাকতও আমার নেই।
এখন কথা হলো, যে গানের সুর, তাল, লয় কিছুই জানি না, শুরুতেই সে গান আমি গাইতে গেলাম কেন? যে সব শব্দ আমার স্মৃতিভা-ার থেকে হারিয়ে গেছে অথবা যাচ্ছে, যেগুলো আমি ভুলেও বলি না, শুনিও না, তা নিয়ে আজ এত বছর পর কেন এত মাতামাতি! কী কারণে এই সময়ে দূর পরবাসে ন্যাশভিলে বসে আমি ‘জিয়াফত’ ও ‘তামদারির’ কথা ভাবছি এবং লিখছি। যাঁদের জন্য লিখছি তাঁরাও জীবনে এমন অপরিচিত শব্দ সমূহের সাথে আদৌ কোনও দিন পরিচিত হয়েছেন কি না তাও আমি নিশ্চিত নই। তবু কেন এই উদ্যোগ, কেন এই প্রচেষ্টা! উত্তরে আপাতত এটুকু বলে রাখি, উদ্দেশ্য একটা আছে বটে এবং মন খুলে এ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আজ দু’কথা বলতেও চাই, পারব কি না জানি না, না পারলেও অন্তত একটা ইশারা দিয়ে যাব। ততক্ষণ ধৈর্য ধরুন, শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকুন, দেখা যাক কী হয়। রচনাটি যখন শুরু হয়েছে, এক জায়গায় গিয়ে শেষ তো হবেই। তার আগে আমার দাদীর জবান থেকে পাওয়া শব্দগুলো সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কিছু বক্তব্য, অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকাহিনির একটি সংক্ষিপ্ত বয়ান এখানে তুলে ধরতে চাই।
আভিধানিক অর্থে ‘জিয়াফত’ এবং ‘তামদারি’ অভিন্ন হলেও, আমার দাদী এ দু’টো শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এস্তেমাল করতেন। কেন করতেন, সে প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। তিনি নাম-দস্তখত জানতেন না, জনমে কোনও দিন স্কুলেও যাননি। জীবনে যা শিখেছিলেন তার সবই মুরব্বিদের কাছ থেকে শুনে শুনে, আপন চোখে দেখে দেখে এবং দুই হাতে কাজ করে করে। বাকিটুকু রপ্ত করেছিলেন নিজের বিদ্যাহীন বুদ্ধি খরচ করে! আর এখানেই তিনি ছিলেন আর দশ-পাঁচ জন থেকে আলাদা! সময়-¯্রােতের উল্টোদিকে গিয়ে বৃদ্ধা এই বিধবা নারী আরও অনেক আজব আজব শব্দ হরহামেশাই বলতেন এবং তাঁর মতো করে ব্যবহারও করতেন। আমাদের বুঝতে কোনও অসুবিধাও হতো না। যেমন – চিংড়িকে বলতেন, ‘শুঁড়আলা মাছ’; তাঁর কাছে ‘বাতাস’-এর প্রতিশব্দ ছিল, ‘বয়ার’; ডিমকে ‘বইদা’, ‘শিং’ ও ‘মাগুর’ মাছকে বলতেন, ‘বয়লা’ মাছ; কোনও জায়গায় গিয়ে দিনে দিনে ফিরে আসা তাঁর ভাষায় ছিল ‘হাজম যাওয়া’, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমার দাদী ছিলেন রাজাবিহীন তাঁর আপন রাজ্যের স্বঘোঘিত রানী। তিনিই প-িত, তিনিই ভাষাবিদ, তিনিই তাঁর আপন ভাষার চর্চ্চাকারিনী! কোন কর্তৃত্ববলে তিনি ‘জিয়াফত’ ও ‘তামদারি’-তে নিজের মগন করে আলাদা আলাদা অর্থ আরোপ করেছিলেন! এ সওয়ালের জওয়াব দেওয়ার সাধ্য আজ কার আছে!
‘জিয়াফত’ বলতে তিনি বোঝাতেন, স্বল্প পরিসরে বাড়িতে ১০/২০ জন আত্মীয়স্বজন অথবা পাড়া-পড়শি মেহমানদের দাওয়াত করে খাওয়ানো। খৎনা অথবা বিয়ে উপলক্ষে ‘জিয়াফত’-এ অতিথিদের সংখ্যা ৫০/৬০, এমন কি ১০০/২০০-তেও গিয়ে ঠেকতো। এ অনুষ্ঠানের রান্নাবান্না এবং খাওয়াদাওয়া হতো ঘরের ভেতরে, নয় তো বা বড়জোর বাড়ির উঠোনে। দাদীর অভিধানে এটাই ছিল ‘জিয়াফত’-এর সংজ্ঞা ও তার চৌহদ্দি। উপলক্ষের রকম ভেদে ‘জিয়াফত’-এ খাবারের গুণমান নির্ভর করত। যেমন বিয়ে কিংবা বিয়েসংশ্লিষ্ট ‘জিয়াফত’ হলে কোর্মা-পোলাও, দুধ-দই, মিঠাই থাকা চাই। অন্য ধরনের ‘জিয়াফত’-এ সাদা ভাত, আলু-গোশÍই যথেষ্ট। ‘জিয়াফত’-এর একটি প্রধান অনুষঙ্গ ছিল, বাড়িতে এক বা একাধিক ছাগল জবাই করা। কদাচিৎ যে গরু কাটা হতো না, সে কথাও বলা যায় না। তবে কোনও ‘জিয়াফত’-এ-ই মাছ, নিরামিষ, ডাল, শাক-সবজি, ইত্যাদি পরিবেশন করার চল ছিল না।
‘জিয়াফত’ আয়োজনে কুটনা কোটা, ধোয়াধুয়ি, রান্নাবান্নার আঞ্জামের জন্য দাদী, মা-চাচী এবং বাড়ির কাজের লোকজনই যথেষ্ট ছিলেন, তবে উৎসবযজ্ঞ বড় হলে, গ্রামের আশপাশ বাড়ির নারী-পুরুষ এসে পেটেভাতে কাজ করে দিয়ে যেতেন। সে কালে এ সব কাজে আনুষ্ঠানিক ভাবে মজুরি দেলদেনের কোনও রেওয়াজ ছিল না। আজকাল বাড়িতে বাড়িতে বড় ‘জিয়াফত’ আর হয় না বললেই চলে, হলেও মোটা টাকায় শহর থেকে ‘ডেকোরেটার’ ভাড়া করে আনতে হয়। অর্থ ছাড়া এ জাতীয় কাজে গ্রামে আর সাহায্যকারি মিলে না। যদি যান সেখানে, দেখতে পাবেন, পয়সা দিয়ে ‘বাঘের দুধ’ মিলে, কিন্তু বিনে পয়সায় কপালে একটি গালিও জুটে না।
খাওয়াদাওয়া এবং উৎসব-আমেজ ছাড়াও ‘জিয়াফত’-এর আরও কিছু অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ছিল। যেমন – এর ফলে পারিবারিক সম্পর্ক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হতো, পারষ্পরিক জানাজানি ও বোঝাবুঝি উত্তরোত্তর নতুন মাত্রা লাভ করত। পরিবারে পরিবারে রেষারেষি, ভুল বোঝাবুঝি, গাল ফোলাফুলি, ইত্যাদি দূর হতো। আবার অনেক সময় ‘জিয়াফত’-এ হিতে বিপরীতও হতো। কাকে কে দাওয়াত দিল, কাকে আগে দিল, কাকে পরে দিল, কে খেতে পেল, কে পেল না, ইত্যাদি যখন ফেৎনায় রূপ নিত তখন জিয়াফতের মূল উদ্দেশ্য ল-ভ- হয়ে ধুলায় লুটাত। আমাদের বাড়িতে এমন অঘটনও ঘটতে দেখেছি।
এ বার আসি ‘তামদারি’-র কথায়। দাদীর মতে, ‘তামদারি’ আরও অনেক বড়, বিশাল বড় ব্যাপার! এ উপলক্ষে ডজন ডজন বড় বড় গরু জবাই করা হয় এবং দিন-রাত ধরে দু’-চার-পাঁচ হাজার মানুষের আপ্যায়নের আয়োজন চলে। এ এক বিরাট আনন্দ উৎসব। ঘরে অথবা বাড়ির আঙ্গিনায় এর স্থান সংকুলান হয় না, হওয়ার কথাও নয়। ‘তামদারি’-র কাল ও স্থান নির্ধারিতই ছিল যথাক্রমে পৌষ-মাঘ মাসে উন্মুক্ত মাঠে আমন ধান ওঠার পর। মেঘ-বৃষ্টির মাঝে তো আর বাড়ির বাইরে এত বড় আয়োজনের ঝুঁকি নেওয়া যায় না। ‘তামদারি’-র আয়োজক-উদ্যোক্তা থাকতেন, হয় কোনও স্থানীয় জমিদার, নয় তো বড় ধনী পরিবার। এক বা একাধিক গ্রামের বাসিন্দা যৌথ ভাবেও এ জাতীয় বড় আয়োজনের দায়িত্ব নিতেন। সে ক্ষেত্রে সবাই মিলে চাঁদা তুলে আরও পাঁচ-দশ মৌজার মানুষকে দাওয়াত করে খাওয়াতেন। খাওয়াদাওয়া হতো মাটিতে, শুকনো খড়ের উপর বসে লাল রঙের মাটির সানকিতে কিংবা চকচকানো পাতলা সবুজ কলাপাতায়। শীতের মৌসুমে ধানক্ষেতে বসে কলাপাতায় ঝোলেভাতে খাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়! এটাও একটা শিল্পকর্ম, তাকে কোশেশ করে রপ্ত করতে হতো!
খাবারদাবার রান্নার জন্য বড় বড় ডেকচি পাতিল, লম্বা হাতলওয়ালা কাঠের চামচ, ইত্যাদি সরঞ্জাম দূর দূরান্তের এ-বাড়ি ও-বড়ি থেকে চেয়ে আনা হতো। এ জন্য কোনও ভাড়া কিংবা টাকাপয়সা গুনতে হতো না। তবে অনুষ্ঠান শেষে ধুয়ে মুছে ফেরত দেওয়ার সময় চেয়ে আনা বড় ডেকচির ভেতর মাটির পাতিলে শুভেচ্ছা সরূপ ‘ভাত-তরকারি’-র হাদিয়া দেওয়া হতো। অবশ্য এই রেওয়াজেও কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। এগুলো ছিল সে যুগে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত ঐচ্ছিক সামাজিক রীতিনীতিরই অংশ। আজ সেই সামাজিকতাও নেই, নিয়মনীতিরও বালাই নেই। বাংলাদেশের এ সব সুন্দর সুন্দর সংস্কৃতির অবশিষ্টাংশ আপন আপন অস্তিত্ব হারিয়ে ইতিহাসের সংরক্ষিত কোঠরিতে গিয়ে নিরাপদে আশ্রয় নিয়েছে! এ সব যেন এখন সুদূর অতীত! সেগুলো আর আমাদের জীবনের অনুষঙ্গ নয়, আমাদের কিছইু নয়, কেবলই সমাজতত্ত্ববিদদের গবেষণার বিষয়বস্তু! তবু আফসোস নেই, হোক না গবেষণা, তাতে যদি নতুন কিছু জানা যায়, শেখা যায়, সমাজের যদি কোনও উপকার হয়, ক্ষতি কী।
‘তামদারি’ শুরু হতো আগের দিন আসরের নামাজের পর গরু জবাইয়ের মাধ্যমে। গোশÍ কাটাকাটি, ধোয়াধুয়ি ও মসলা বাটার কাজে পাড়া প্রতিবেশীর নারীকর্মীরা দলে দলে এসে যোগ দিতেন। কাউকে কাউকে ডেকে আনা হতো, আবার অন্যরা খবর পেয়ে স্বেচ্ছায় এসে এমন নেক কাজে যোগ দিতেন। রান্নার জন্য কিছু বাবুর্চিকে দাওয়াত করে আনা হতো, খবর পেয়ে বাকিরা আশপাশ গ্রাম থেকে কোনও কোনও সময় দূর দূরান্ত থেকেও বিনা দাওয়াতে স্বপ্রনোদিত হয়ে আসতেন। বাবুর্চিরা এবং যোগালেরা সবাই স্বপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তারা কোনও বিদ্যালয়ে পড়েননি, দেখে দেখে এবং হাতে কলমে কাজ করে করে এমন দক্ষতা অর্জন করতেন। তাঁরা সবাই স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পেশাদারিত্বের সাথেই কাজ করতেন। কেমন দিনে, কেমন মানুষ ছিলেন তাঁরা! একটি সামাজিক উৎসবে এসে কর্মময় নির্ঘুম রাত কাটিয়ে, ২৪ ঘন্টা পর মনে প্রশান্তি ও আত্মতুষ্টির এক মহাভা-ার নিয়ে সবাই খালি হাতে বাড়ি ফিরতেন! এমন মানুষের মন, সমাজ ও সামাজিকতা আজ কোথায় পাবেন!
ছোটবেলা এ ধরনের বেশ কিছু ‘তামদারি’-তে আমি গিয়েছি। কোনও সময় আব্বার সাথে, কোনও সময় ‘চটর’-চাচার (বাড়ির কাজের লোক) হাত ধরে ধরে, এমনও হয়েছে, বাড়ির নিকটে একা একাই চলে গিয়েছি, মজা করে পেট ভরে খেয়েছি এবং খুশিমনে মায়ের কোলে ফিরে এসেছি! এ রকম এক ‘তামদারি’র কথা আজ আবছা আবছা মনে পড়ছে। আমাদের প্রতিবেশী গ্রাম ‘কাঞ্চনপুর’-এর পশ্চিমে ‘ঘুর্নির বন্দ’-এ (সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় ‘বন্দ’ মানে মাঠ) ‘তামদারি’-র আয়োজন চলছে। ওই মাঠে মাঝে মাঝে ঘোড়দৌড়ও হতো। একবার আমি তাও দেখতে গিয়েছিলাম। শুধু আনন্দ-উৎসবই নয়, আমাদের অঞ্চলের জন্য একটি অতি বেদনাদায়ক দিনের স্মৃতি এই ‘বন্দ’-এর হাওয়ায় অনেক দিন ধরে মিশে আছে, আজও হাহাকার করছে! জমির আল ঠেলাঠেলি নিয়ে দুই দলের মাঝে এই ময়দানে রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয়েছিল এবং কোচের খোঁচায় কাঞ্চনপুরের ‘নজই’ মারা গিয়েছিল। তার পর থানা-পুলিশ মামলা-মোকদ্দমা চলছে কয়েক বছর! সেখান থেকে মাইল খানেক উত্তর-র্পূব দিকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার পাশে আছে এক বাজার। বাজারের গা ঘেষে আছে ছোট্ট আরেকটি মাঠ। সেখানে হতো ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই; তাও উপভোগ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। পঞ্চাশ-ষাট-এর দশকে বৈচিত্র্যে ভরা ছোটবেলাকার কী সুন্দর দিনগুলো পেছনে ফেলে এসেছি! আফসোসের সাথে বলতে ইচ্ছে করে,
‘দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না,
সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি’।
ফিরে আসি ‘তামদারি’-র কথায়। যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমি ক্লাস ফোর/ফাইভ-এ পড়ি। আম্মা বিকেল বেলা আমাকে গোসল করিয়ে, মাথায় তেল মেখে, চুল আঁচড়িয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে দিলেন। আমি একা একা গেলাম। পথ চিনাচিনির কোন দরকার পড়েনি। বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখি, চারদিক থেকে মানুষের ঢল – ছুটছে ‘ঘুর্নির বন্দ’ বরাবর। আমি পথচলা মানুষদের ¯্রােতে ভেসে ভেসে অকুস্থলে গিয়ে হাজির। মাঠে গিয়ে মানুষের ছয়লাব দেখে একটু ভয় পেয়েছিলাম! এত মানুষের মাঝে যদি হারিয়ে যাই, আমাকে যদি কেউ ধরে নিয়ে যায়, তা হলে হবেটা কী! তবে জায়গাটা আমাদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে ছিল না। মাত্র আধ-মাইল কিংবা তার চেয়েও কম। খাওয়ার পালা তখনও শুরু হয়নি, মাঠে মানুষ আর মানুষ! তারপরও আগমনী মানুষের আসা বন্ধ হচ্ছে না! দেখতে দেখতে এক সময় সবার সাথে লাইন ধরে খড়ের উপর বসে পড়লাম। প্রথমে পেলাম মাটির সানকি, তারপর এক মেয়ে চিমটি চিমটি করে নুন দিয়ে গেল। এই যে গেল, তো গেল! আর তো কেউ আসে না! এ দিকে খিদেয় পেট মোচড় মারছে। এর পর ডান দিকে বেশ দূরে দেখতে পেলাম, কাঁচা বাঁশবেতের তৈরি সাদা টুকরিতে করে লাল ভাত বিলি করছেন তিন জন। দুই জন টুকরি ধরছেন, আর এক জন খালি হাতে মুঠি ভরে ভরে পাতে পাতে ভাত তুলে দিচ্ছেন। এ ভাবে কিছুক্ষণের মাঝে ভাত বন্টনকারি আমাকে পার হয়ে গেলেন। ভেবেছিলাম, তরকারি পেতে আরও অনেক দেরি হবে। কিন্তু না, তা হলো না। মোটামুটি অল্প সময়ের মাঝেই দেখলাম, একটি মাঝারি মাটির পাতিল থেকে একটি ছ্ট্টো বাটি দিয়ে তুলে তুলে ঝোল সহ গোশÍ দিয়ে যাচ্ছেন আরেক জন। দেখতে দেখতে আমার সানকিতে সুস্বাদু গরম গোশেÍর তরকারি পড়ল। এত গোশÍ আমার ভাগ্যে আগে আর কোনও দিন জুটেনি। মুহূর্তের মধ্যে মাটির সানকি যেন আমার কাছে সোনার থালার চেয়ে মূল্যবান হয়ে উঠলো! আমি তো আহ্লাদে আটখানা! হাত না ধুয়েই শুরু করে দিলাম। পরে দেখলাম, হাত ধুয়ানোরও একটি ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এলামোলো আয়োজনের জন্য ওই সেবা সে দিন আমার নসিব হয়নি।
লাল ভাত, গরু গোশÍ দিয়ে খুব মজা করে খেলাম! খাওয়ার পর এখন পানি পাই কোথায়! পানির খোঁজে এ-কে ও-কে জিজ্ঞেস করে গিয়ে হাজির হলাম, একটু দূরে মাঠের এক কোণে। গিয়ে দেখি এক এলাহি কা-। একটি খোলা নৌকাকে বিল থেকে তুলে ধুয়ে মুছে সাফ করে কাঁধে করে বয়ে এনে রাখা হয়েছে খোলা মাঠে। আর গ্রামের পুকুর থেকে ছেলে, বুড়ো, নারী, পুরুষ, সকলে মিলে নৌকার পেট ভরে পানি জমা করছেন। কেউ কলসিতে করে, কেউ বালতি বয়ে, কেউ এলুমিনিয়ামের জগ দিয়ে, কেউ বদনাতে করেও খাবার পানি তুলে আনছেন! কে জানে, এ কাজে লাগানোর আগে বদনাটা কি ভালো করে মাজাঘষা হয়েছে! ভাগ্যিস, লোটা বা ঘড়া হলে তো
‘জল’-ই হয়ে যেত এবং ‘জল’-‘পানি’ মিলে কী যে হতো, কে জানে! আজকের এই বয়সে এসে, ‘ঘুর্ণির বন্দ’-এর ওই ছবিটি যখন আমার চোখের সামনে ভাসে তখন ভাবি, সর্বগ্রাসী আগুন নেভানোর জন্য গ্রামবাসী যে ভাবে যার যা আছে তাই দিয়ে পানি এনে অনলে ঢালে, ঠিক সে ভাবেই যেন সেই দিন সেই ‘তামদারি’-তে মানুষের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এলোপাতাড়ি পানি এনে ঢালা হচ্ছিল আলকাতরা মাখা কাঠের নৌকায়। আরও ভাবি, গ্রামের মানুষের কী অদ্ভূত উদ্ভাবনী শক্তি! সে কালে এর কী কোনও বিকল্প ছিল?
খোলা হওয়ায় উন্মুক্ত পরিবেশে ‘তামদারি’-তে আসা অতিথিদের মাঝে কথাবার্তা, গল্পগুজব, ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ খুব একটা থাকে না। যাঁরা খান, তাঁরা পেট ভরে তৃপ্তি পান, যাঁরা খাওয়ান তাঁরা সওয়াব হাসিল করে তৃপ্তি পান। কোন তৃপ্তির মূল্য কার কাছে কতখানি সেটা মাপা বড় কঠিন!
এর বাইরে আরেকটা ব্যাপার আছে। কিছুক্ষণের মতন মানুষের মাঝে মানুষের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে হারিয়ে যাওয়ায়ও একটা অনাবিল আনন্দ আছে! অবর্ণনীয় তৃপ্তি আছে! কিন্তু এই কিসিমের তৃপ্তির স্বাদ কত জনের ভাগ্যে জুটে, বলা মুশকিল! সেই দিন অল্প বয়সে এই সব তত্ত্বকথা আমার মনের কোণে উদয় হয়নি। তবে ‘তামদারি’-র অন্য একটি বৈশিষ্ট্য আমাকে অভিভূত ও আপ্লুত করেছিল। মানুষের দৌড়াদৌড়ি, কোলাহল, কলরব এবং অসংখ্য মানুষের এক সাথে কথা বলার গম গম আওয়াজ আমার কানে গানের মতন সুরেলা তরঙ্গ তুলেছিল, যে সুরের মধুর ধ্বনি সময় সময় আজও আমার কানে বাজে!
‘তামদারি’-র শেষ পর্যায়ে ‘ঘুর্নির বন্দ’-এ ঘটে যাওয়া আরও দু’টো ঘটনা বিশেষ ভাবে আমার দৃষ্টি কাড়ে। এক কোণে দেখলাম নারী-পুরুষ মিলে মুষ্টিমেয় কয়েক জন ফকিরমিসকিন জটলা বেঁধে হাত বাড়াচ্ছেন আর তাঁদেরকে ভাত-গোশÍ দেয়া হচ্ছে। কারও হাতে মাটির বাসন, কারও আছে জং পড়া এলুমিনিয়ামের প্লেট, কারো কাছে কলাপাতা, যাঁর হাতে কিছু নেই, তিনি তাঁর শাড়ির আঁচল পেতে দিচ্ছেন দু’মুঠো অন্নের জন্য। পরনের কাপড় ভাতকে ধারণ করতে পারলেও তেল ও মসলা মিশ্রিত গোশেÍর ঝোল টপ টপ করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে! এ ভাবেই স্বচ্ছলের আহার নিরাপদে পেটে যায়, আর কাঙালির ধন মাটিতে লুটায়! তবু যা থাকে, তাই বা কম কী! আরও লক্ষ করলাম,
‘তামদারি’-তে মানুষের সাথে কুকুরেরও শরিক হওয়ার সুযোগ থাকে। তারাও জড় হয়, ঘেউ ঘেউ করে, উচ্ছিষ্ট খায়, হাড়গোড় নিয়ে টানাটানি করে।
আজকের বাংলাদেশে প্রতি দিন অন্য কিসিমের এক ‘তামদারি’ চলছে। এ ‘তামদারি’-তে শুধু খাস মেহমানরাই দাওয়াত পায়। যারা আসে, তাদের এক দল শুধু খায়, পেট ভরে খায়। আরেক দল আঁচল পেতে নিয়ে যায়, কিছু ঝরে যায়, বাকিটা তুলে রাখে, জমা করে। অন্যরা টানাটানি করে, মারামারি করে, খায়ও বটে!
অক্টোবর ৩০ ২০১৯
লেখকঃ অধ্যাপক, টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটি, ন্যাশভিল, টেনেসি, ইউএসএ