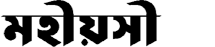শেলী জামান খান
(১)
সাজেদা জামান বিরু। বিক্রমপুরের মেয়ে। গ্রামের নাম কলমা। থানা লৌহজং।বাবা আব্দুল হাই পাঠান। পাঠান সাহেব ছিলেন কলমা গ্রামের চেয়ারম্যান। অত্যন্ত গন্যমান্য লোক। কলমা, পাঠানবাড়ির সেই মেয়ের আমেরিকান জীবনও প্রায় সাত বছরের। বছরের হিসেবে তার বয়স আশি হলেও, তিনি বসে খেতে একদম রাজি নন। শাওয়ার শেষে নিজের পরার কাপড়টা নিজ হাতে ধুয়ে ফেলেন। টেবিলে বসে ছুঁড়ি, কাঁচি দিয়ে পেঁয়াজ, রশুন সবজি কাটেন, রুটি বেলেন গোল করে। তিনি উত্তর আমেরিকা প্রথম আলোর একনিষ্ট একজন পাঠিকা। হয়েছিলেন, প্রথম আলোর পিঠা উৎসবের বিচারক।পরিবারের সদস্যদের বিশেষ বিশেষ দিনে তাদের নামে কবিতা লিখে চমকে দেন বিরু!
দীর্ঘ লকডাউন, আইসোলেশন এবং কোয়ারেনন্টিনের যাঁতাকলে গৃহবন্দী থাকলেও নখদর্পনে রাখেন বিশ্ব সংবাদ। মহামারির খবর, আমেরিকার নির্বাচন, বাংলাদেশের পদ্মা সেতু, মেট্রোরেলের কাজের অগ্রগতি জানতে চান আগ্রহ ভরে। শোনেন দেশের নানা খবরাখবর।
করোনা মহামারি শুরু হলে নিজে যেমন সতর্ক ছিলেন, তেমনি সতর্ক করতেন সবাইকে। কিন্তু বিধি বাম হলে, হঠাৎ আসা জ্বর, ঠান্ডা, কাশি ও খাবারে অরুচি জনিত অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে যেতে বাধ্য হলেন। রেপিড টেস্টে ধরা পড়ল কোভিড-১৯ পজিটিভ। আমাদের ছয় বোন একমাত্র ভাইয়ের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এতো সতর্কতার পরও ‘মা’ কোভিড-১৯ ভাইরাসটির আক্রমণ এড়াতে পারলেন না । এই বয়সে কোভিড! মা কি পারবেন এই যুদ্ধে জয়ী হতে? ভাইরাসকে পরাজিত করতে? হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরতে?
আমাদের সবার মনে নানাবিধ ভয়, আশংকা। কারন আমাদের আব্বা অত্যন্ত আকস্মিকভাবে, বিনা নোটিশে, অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এখন মা’ই আছেন আমাদের নাড়ীর বন্ধন হয়ে। কিন্তু আমাদের সকল আশংকার, সকল প্রশ্নের খুব ভালো উত্তর দিলেন আমাদের মা। নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ড জুইশ হাসপাতালে, একটি বিজাতীয় ভাষার দেশে, নার্স, ডাক্তারদের তত্তাবধানে কাটালেন দশ দশটি দিন।তারপর ফিরে এলেন কোভিডকে জয় করে।
আমাদের নানা, খালা, মামারা এবং আব্বা চলে যাবার পর, আমাদের মা’র ‘বিরু’ নামটি ধরে ডাকার আর কেউ ছিল না এই পৃথিবীতে। একসময় আমার বড় ছেলে সুমিত তার নানুকে ডাকতে শুরু করলো ‘বিরু’ নামে। সে বললো, একজন মানুষের নাম তার জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। মানুষটির সাথে সাথে তার নামটিকেও বাঁচিয়ে রাখতে হয়।
সুমিত প্রায়ই লসআ্যান্জেলস থেকে ফেইসটাইমে ফোন করে। কথা বলে বিরুর সাথে। ‘বিরু কেমন আছো?’ বাক্যটি শুনলেই আমার মনে পড়ে যায় আমাদের আব্বার কথা। বিরু হাসিমুখে নাতির প্রশ্নের উত্তর দেন। বলেন, ‘তুমি কেমন আছ? নাতবৌয়ের মুখ কবে দেখাবা? নাতবৌ না দেখেই কি চলে যেতে হবে নাকি? ‘
‘কিযে বল, তুমি এতো তাড়াতাড়ি কই যাবা? লসআ্যন্জেলস বেড়াবা তোমার নাতবৌ এর সাথে।’
বিরু উদাস কণ্ঠে বলেন, ‘করোনায় কত মানুষ চলে গেল, কবে যে চলে যেতে হবে, জানি না।’
নাতি বলতো, ‘তুমি কোথাও যাবে না বিরু, মহামারি শেষ হলেই আমি আসবো। আমাদের আবারো দেখা হবে’। তারপর কাব্য করে বলতো,
“আমাদের দেখা হবে মহামারি শেষে।
আমাদের দেখা হবে জিতে ফিরে এসে।”
সত্যি, সত্যিই বিরু জিতে ফিরে এলেন। আমরা ঘটা করে, লাল গোলাপের তোড়ায় তাঁকে বরণ করলাম। রেড ওয়াইনের গ্লাস ঠুকে বললাম,
“চিয়ার্স টু বিরু!
বিরু গালে টোল ফেলে হাসেন!
মা হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন প্রায় দুই সপ্তাহ। ধীরে ধীরে রিকভার করছেন। যেখানে আমার নিজেরও পুরোপুরি রিকভার করতে মাসখানেক সময় লেগেছিল। মা’র সেবাযত্ন করতে করতে আজকাল অনেক গল্প করি আমরা করোনা জয়ী দুজন মানুষ। মা ও মেয়ে।
এমন করে, মায়ের ফেলে আসা জীবনের গল্প, সুখদুঃখের গল্প শোনার বহুকাল সময় হয়নি আমার। মহামারির এই অবকাশে মায়ের স্মৃতিচারণ শুনি। আনন্দ নিয়ে, উৎসুক হয়ে শুনি। বড় ভালো লাগে। এমন করে পুরনো দিনের গল্প বলার মানুষগুলোর অনেকেই চলে গেছেন। অনেকেই যেকোন সময় চলে যাবেন। একসময় হারিয়ে যাবে এইসব গল্পগুলোও। অতীত হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর নাম আমরা হয়তো ধীরে ধীরে একদিন ভুলে যাবো।
(২)
আমার মা স্মৃতিচারণ করতে করতে তার ফেলে আসা দিনগুলোতে ফিরে যান…!
তিরিশের দশকের গ্রাম। গ্রামটি মোটামুটিভাবে শান্তিপূর্ণ। বর্ধিষ্ণু। গ্রামের বেশীর ভাগ মানুষ কৃষক এবং ব্যাবসায়ী। গ্রামে মোট জনগোষ্টির মধ্যে হিন্দু মুসলিমের সংখ্যা প্রায় সমান সামন। পদ্মাপাড়ের এইসব গ্রামগুলো নদীবিধৌত ও জোয়ার-ভাটা দ্বারা প্লাবিত নিম্নাঞ্চল। অন্যসব নদী দূরবর্তী অঞ্চল থেকে এই অঞ্চলের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।ভাটি অঞ্চল বলেই এখানে ছয় মাস পানি আর বাকি ছয় মাস থাকে শুকনো মৌসুম।
গ্রামের বর্ষাকালের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। বৈশাখ মাস আসতে না আসতেই পদ্মা নদীর পানি ফুলে ফেঁপে উঠে। ফুঁসে উঠে প্রমত্তা পদ্মা। প্রচন্ড আবেগে ঝাপিয়ে পড়ে জনপদের উপর। ভেসে যায় গ্রামের মাঠ, ঘাট, পথ, পুকুর, বাড়ির উঠোন। বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে তখন কেবল পানি আর পানি। প্রবল ঠেঁউয়ের তোড়ে কোনক্রমে মাথা উঁচু করে আকণ্ঠ দাঁড়িয়ে থাকে বিশাল বিশাল হিজল, তমাল, বট-পাঁকুড়ের গাছগুলো। কোষা বা ডিঙ্গি নৌকায় পারাপারের সময় চোখে পড়ে ভাসমান হিজল ফুল। কচুরীপানার দল।
পানি আসার আগেভাগেই ধান মাড়াই, চাল, সব ধরনের ডালে গোলা ভরা হয়ে যায়। ঘানিতে শর্ষে ভেঙ্গে তেলের জালাগুলো ভরা হয়। প্রায় মাস ছয়েকের খাবারের যোগান হাতে করে গাঙ্গের ঢল আসার সাথে সাথে ঘরে উঠতে হয় গ্রামবাসীর।
ঢলের পানি উঠোন ছাপিয়ে ওঠার আগেই বাড়িতে বাড়িতে তৈরি হয়ে যায় বাঁশের তৈরি সাঁকো। আব্দুল হাই পাঠান কলমা গ্রামের চ্যায়ারম্যান হলে কি হবে, তার বাড়ির চিত্রও ছিল একইরকম। পাঠান সাহেবের বাড়ির উঠোন জুড়েও তৈরি হয় বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকোর থাকে নানা শাখা-প্রশাখা। বড় ঘর থেকে ভেতর বাড়ির আরও দু’টো সম্প্রসারিত শোবার ঘর, পাকের ঘর, পায়খানা, মেয়েদের স্নানঘর, সর্বত্রই যেতে হয় সাঁকো পারাপার করে। স্বয়ং পাঠান সাহেব, বাড়ির অন্য পুরুষ সদস্য এবং চাকরবাকরদের জন্য সাঁকো তৈরি করা হয় বাহির বাড়ির বাংলাঘর, বাংলাঘর থেকে বাড়ির মসজিদ পর্যন্ত।
বর্ষাকালে জরুরী প্রয়োজনে পাড়া প্রতিবেশীর বাড়ি, ডাক্তার-কবিরাজ বা শহর-গন্জে যেতে হলে বাংলাঘরের সাথেই বাঁধা থাকে একটি দুটি কোষা নৌকা। পাঠান সাহেব নিজে বা পরিবারের মেয়েদের জন্য বরাদ্দ বড় একটি ছৈতোলা নৌকা। সেই নৌকার পাটাতন দামী কাঠের।তার মসৃন পাটাতনের উপর গালিচার বিছানা ও তাকিয়ায় ঠেঁস দিয়ে বসার ব্যাবস্থা।এমন বড়সড় এবং সুসজ্জিত নৌকা গ্রামে কেবল দুই একটির বেশী নেই।
বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত গাঙ্গ থেকে আসা ঢলের পানি জমে থাকে লোকালয় জুড়ে। তখন অলস বসে থাকা ছাড়া করার কিছু নেই। অনেকেই অবশ্য এই সময়টায় বেত দিয়ে ডালা, কূলা, ঝুড়িঁ বোনেন।পাটি, মাদুর বোনেন। মেয়েরা সেলাই, সূচিকর্মে ব্যস্ত থাকে।
কার্তিক মাস শরু হতেই কৃষক এবং বর্গাচাষী পরিবারগুলোর কাজকর্ম এবং ব্যাস্ততা শুরু হয়ে যায়। কার্তিকের শুরুতেই ঢলের পানিতে হঠাৎ করেই টান ধরে। ধীরে ধীরে সেই আঠাঁই পানি লোকালয় থেকে নেমে আবারও পদ্মার বুকে ফিরে যায়। গ্রামের পথ, ঘাট, জমিজমা, প্রান্তর আবার জেগে ওঠে। মাঠে, ঘাটে, ফসলের জমিতে গজিয়ে উঠতে শুরু করে কচি দূর্বা ঘাস, লাঠিভাঙ্গা শাক, আরও কত কি! চারিদিকে সবুজ আর সবুজ। শুরু হয় সবুজের সমারোহ। চাষিরাও ব্যাস্ত হয়ে পড়েন ফসল ফলাতে। ধান, পাট, নানা রকমের ডাল, শর্ষে, তিল, কাউন, মরিচ, লাউ, কুমড়ো, সীম, আরও কত রকমের মৌসুমী সবজিতে ভরে ওঠে কৃষকের ক্ষেত, গৃহস্থের আঙ্গিনা। এই শুকনো সময়টুকু খুব ক্ষণকালের। তাই গ্রামবাসী সবার মধ্যেই এই সময়টুকু কাজে লাগানোর প্রবল একটা তাড়া থাকে।
শুকনোর দিনে পাঠান বাড়ির মেয়েরা বেড়াতে যায় ‘মাফা’ বা পালকিতে চড়ে। কাছাকাছি কোথাও বা এপাড়া থেকে ওপাড়া যেতে ব্যাবহার করা হয় ‘ডুলি’। সাধারণ লোকজন চলে পায়ে হেঁটে। মাইলের পর মাইল।যানবাহন নিয়ে সেইসময়ের প্রচলিত একটি কথা ছিল, “বর্ষায় নাও, শীতে পাও”।শুকনোর দিনে এদিকসেদিক যাতায়াত একটু সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টকর হওয়ায় বর্ষাকালেই আত্বীয়-স্বজনদের বাড়ি যাতায়াত বেড়ে যায়। বাড়ে কুটুম্বিতা! বাড়ির বৌঝিরা পিঠাপুলি বানিয়ে, রান্নাবান্না করে টিফিন ক্যারিয়ার বোঝাই খাবার নিয়ে নৌকায় চড়ে আত্মীয় বাড়ি যান লম্বা সময়ের জন্য কুটুম হতে।
(৩)
বিশাল পাঠান বাড়ির মোট তিন শরীক। আলিমুদ্দিন পাঠান। ঈদু পাঠান। সামাদ পাঠান।এরা তিন চাচাত ভাই পাঠান বাড়ির প্রধান পুরুষ।
আলিমউদ্দিন পাঠান। পিতার একমাত্র সন্তান। বিয়ে করেছিলেন কাজী কসবা’র বিখ্যাত “বাবা আদমের দরগাবাড়ি” পরিবারে। আলিমউদ্দীনের স্ত্রী ফরহাতন নেসার রূপ ছিল ভূবন ভোলানো। ফরহাতনের কোল জুড়ে এলো এক পুত্র। পুত্রের নাম রাখা হল আব্দুল হাই পাঠান। কিন্তু অচিরেই আব্দুল হাই পিতৃহারা হলেন। একমাত্র নাবালক পুত্রসন্তান নিয়ে অল্পবয়সি, রূপবতী, বিধবা ফরহাতন নেসা, স্বামীর অগাধ সম্পত্তি, টাকা পয়সার একমাত্র মালিক তখন। তাই চারিদিকে তাকে নিয়ে জোড় আলোচনা, ফিসফাস। দফায় দফায় নানা জায়গা থেকে বিবাহের পয়গাম আসতে শুরু করলো। কিন্তু ফরহাতনের বয়স কম হলে কি হবে, বড় কঠিন, অনড় তার চিত্ত। বুদ্ধি তার খুব প্রখর। কেউ তাকে টলাতে পারলো না। দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে তার একটাই জবাব ছিল, তা হল ‘না’। সেই না কেউ ‘হ্যা’তে পরিবর্তন করতে পারেনি।
কিন্তু লেখাপড়া না জানা অল্পবয়সি মেয়ে। এতবড় সম্পত্তির দেখভাল, খোঁজখবর করা মোটেই সহজ কাজ নয়। ফরহাতন বিচলিত হলেন না। তিনি বাপের বাড়ি থেকে নিজের বড় ভাই কাফি খন্দকারকে সপরিবারে নিজের বাড়িতে এসে থাকার অনুরোধ পাঠালেন। ভাই একমাত্র বোনের অনুরোধ ফেললেন না। সপরিবারে এসে উঠলেন বোনের বাড়িতে। বুঝে নিলেন বিধবা বোন ও নাবালক বোনপোর সম্পত্তির দেখভালের দায়দায়িত্ব।
আব্দুল হাই পাঠান দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলেন। জমিজমা, সম্পত্তি রক্ষায় যাতে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ না আসে, তাই ফরহাতন নেসা নিজের আরেক ভাইয়ের মেয়েকেই একমাত্র পুত্রের পুত্রবধু করলেন। পুত্রবধু জেসমিন তার ফুফুর মতই রূপবতী। আব্দুল হাই পাঠান তাকে চোখে হারান। জেসমিন একে একে পাঁচপুত্র তিন কন্যার জন্ম দিলেন। তারপর মাত্র দশ বারো দিন জ্বরে ভুগেই শাশুড়ির জিম্মায় তার সন্তান সন্ততি এবং বিশাল সংসার ফেলে রেখে চলে গেলেন জেসমিন।
ফরহাতনকে এবার ছেলের পুত্রকন্যাদের দায়িত্বও মাথায় নিতে হল। অনেক অনুরোধ এবং চেষ্টা করেও আব্দুল হাই পাঠানকে দ্বিতীয় বিয়েতে সন্মত করানো গেল না। মায়ের মতই তারও জবাব ছিল, সেই ‘না’! সম্পত্তি পাঠান বাড়ির বাইরে অন্যকারো আওতায় আসুক তা সেও চায় না।
দাদি ফরহাতন নেসার তত্তাবধানে বড় হতে লাগলেন, তার নাতি নাতনিরা।ছেলে আব্দুল হাইয়ের তিন কন্যা নূরজাহান, পুস্প এবং বীরু। পুত্ররা হলেন, মন্টু, বিন্দু, সেন্টু, খনু, ধেনু।
বাড়িতে দাস-দাসির কোন অভাব নেই। তবুও ফরহাতন নিজ হাতে একমাত্র ছেলে, নাতি নাতনিদের খাওয়া-দাওয়া তদারক করেন। আব্দুল হাই পাঠান ইতোমধ্যেই তার পিতার সম্পত্তি আরও দ্বিগুন করে তোলেন। তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞানই ছিল সম্পত্তির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ।
আলিমউদ্দীন পাঠানের চাচাত ভাই ঈদু পাঠান। ঈদু পাঠানের একমাত্র ছেলে রশীদ পাঠান। রশীদ পাঠান কোলকাতায় গিয়ে পড়াশোনা করে, চাকরী করতেন পুলিশে। পরে সেখান থেকে আসেন ময়মনসিংহ। রশিদ পাঠানের ছেলেমেয়েরা কোলকাতা এবং ময়মনসিংহ থাকার সুবাদে শিক্ষাদীক্ষায় কেতাদূরস্ত হয়ে উঠেছিলেন খুব। অন্যদিকে আব্দুল হাই পাঠান জমি-জমা’র মোহে আটকে রইলেন। তিনি নিজে বা তার ছেলেমেয়েরা গ্রামে থাকায় শিক্ষাদীক্ষায় তেমন অগ্রসর হতে পারলেন না। সামাদ পাঠানের একমাত্র ছেলে আজিজ পাঠানও রইলেন জমিজমার মোহগ্রস্থ হয়ে।
গ্রামে একটি মাত্র হাইস্কুল ছিল ‘কলমা হাই স্কুল’। ছেলেদের যদিও সেই হাই স্কুল অব্দি পড়ার একটা সুযোগ ছিল, কিন্তু মেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ একদমই ছিল সীমাবদ্ধ।
কলমা হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন, উমেশ বাবু, হেমন্ত বাবু, তুষ্টিবাবু, বিনোদ বাবু নামের হিন্দু শিক্ষকগণ। একমাত্র মুসলিম শিক্ষক ছিলেন আব্দুল হাই পাঠানের স্ত্রীর বড় ভাই মতিউর রহমান।
(৪)
কলমা হাই স্কুলের শিক্ষক বিনোদ বাবুর পাঁচ মেয়ে। বিনোদ বাবুর মেয়েরা বাবার কাছে ঘরেই শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। লক্ষী, শীপু, দূর্গা, বীজু, খনুর আগ্রহে বিনোদ বাবু তার বাড়ি সংলগ্ন কালিবাড়িতে গ্রামের মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল খোলেন।সেই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন বিনোদবাবুর এই পাঁচ কন্যা।অচিরেই সেই স্কুলে গ্রামের মেয়েরা যেতে শুরু করলো। এমনকি বর্ষাকালেও নৌকা করে মেয়েরা স্কুলে যেতে পিছপা হোত না।প্রতিবছরই কালীবাড়ি দীঘির পাড়ে মেলা বসতো। ওখানে দূর্গা পূজা, কালী পূজা, লক্ষী পূজার আসর বসতো। গ্রামের হিন্দু মুসলিম সবাই জড় হোত সেই মেলা এবং পূজায়। সবাই পাত পেতে প্রাসাদ খেতো একসাথে। ঈদগায়ে নামাজের পর সবাই দল বেঁধে এসে খানা খেতো পাঠান বাড়ির বাংলা ঘরে। সেখানে মুসলিমদের পাশাপাশি পাত পড়তো পাড়ার হিন্দুদেরও। কলমা হাই স্কুলের সব শিক্ষকবাবুরা দাওয়াত পেতেন পাঠান বাড়িতে।
পাঠান সাহেবের মেয়েরাও পড়তে যেতেন বিনোদবাবুর মেয়েদের তৈরি সেই ‘মেয়ে স্কুলে’।শুকনোর দিনে পায়ে হেঁটে। অন্যমেয়েদের সাথে দল বেঁধে। বর্ষাকালে নৌকায় চড়ে। কিন্তু একটা সময় কি ঘটলো কে জানে, গ্রামের সাধারণ মানুষ ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দৃশ্যপট গেল বদলে।গ্রামের অনেক প্রসিদ্ধ হিন্দু পরিবার, গোপনে গোপনে বাড়ি, জমি-জিরাত বেঁচে দিতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ একদিন এক সকালে দেখা গেল সিংহবাড়ি, সেন বাড়ি, ভুঁইয়া বাড়ি খালি পড়ে আছে। খা খা করছে তাদের উঠোন। পুকুর পাড়, দর-দালান, ঠাকুর ঘর।
তারপর একদিন যেতেই দেখা যেতো ঐসব হিন্দুবাড়িগুলো পাড়ার কোন প্রভাবশালী মুসলিমের দখলে চলে গেছে। এভাবেই ১৯৪৭, ১৯৫০, ১৯৬৪, ১৯৬৫ সালের দেশ ভাগ, ধর্মীয় দাঙ্গা, যুদ্ধের ফলে গ্রামে একসময় হিন্দুরা সংখ্যা লঘু হয়ে পড়লো। অবস্থাপন্ন, শিক্ষিতহিন্দুরা অনেকেই দেশ ছাড়লেন দেশভাগের প্রথম ধাক্কাতেই। গরীবরাও দেশ ছাড়লেন সহজেই। কারন তাদের হারাবার কিছু ছিল না। কিন্তু শেষঅব্দি রয়েগিয়েছিলেন অল্প কিছুসংখ্যক মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবার।তাদের অবস্থা হল ‘শ্যাম রাখি না কুল রাখি’র মত। এভাবেই একে একে কলমা হাই স্কুলের সব হিন্দু শিক্ষকরাই দেশভাগের তাড়নায় দেশ ছাড়লেন। বিনোদ বাবুরা চলে গেলেন তাদের কন্যাদের নিয়ে। কলমা গ্রামের একমাত্র নারী স্কুলটি বন্ধ হয়ে গেল এক ধাক্কায়।মেয়েদের পডাশোনাও বন্ধ হয়ে গেল!
সাজেদা জামান বিরুর রোগজীর্ণ পাংশু মুখখানি একসময় স্মৃতিকাতর হয়ে উঠলো।অনেকক্ষণ স্মৃতি হাতরে হাতরে বহু কথা বলে একটু সময়ের জন্য থামলেন তিনি।
ছলছল চোখে বললেন, ‘মনে পড়ে, কত কত নাম। কত কত মুখ।কত খেলার সাথী, স্কুলের দিদিমনিদের মুখ। সেসব নিতান্তই শৈশবের কথা। খুব আবছা, ঝাপসা সেসব স্মৃতি। একদম শৈশবে হারিয়েছিলাম মা’কে। এরপর চলে গেছেন বড় দুই বোন। তারপর দাদি ফরহাতন। পরে বাবা। তারপর স্বামী শফীউজ্জামান খান। একে একে নিজের পাঁচটি ভাইও চলে গেল।’ চোখ মুছে বললেন, ‘আমিই কেবল বেঁচে আছি, সবার স্মৃতি আঁকড়ে ধরে। মা, বড় দুই বোন খুব কম বয়সে চলে গেলো, ভেবেছিলাম, তাদের পথ ধরে আমাকেও কম বয়সেই যেতে হবে। কিন্তু হলো তার ঠিক উল্টো।’
মা তার এই সুদীর্ঘ জীবনে মহামারিও দেখেছেন অসংখ্যবার। কলেরা হয়ে গ্রাম ছাড়খাড় হতে দেখেছেন নিজের স্মরনকালেই। পানিশুন্য হয়ে মারা যেতো কলেরা রোগীরা। ঐ সময়ে গ্রামের মানুষের অদ্ভুত একটা বিশ্বাস ছিল, কলেরা রোগীদের পানি খাওয়া বারন। যত পানি খাবে শরীর থেকে পাতলা পায়খানা হয়ে ততই পানি বের হয়ে যাবে, এমনটাই ছিল তাদের বিশ্বাস। এই ভ্রান্তধারনার কারনে কলেরা রোগ দেখা দিলে পানিশুন্যতার কারনে প্রচুর কলেরা রোগী মারা যেতো। তেমনি মহামারিরূপে আসতো ওলাওঠা বা গুটিবসন্ত রোগ। আরও ছিল রাজরোগ যক্ষা। বড় কোন পাপের ফলে হয় কুষ্ঠরোগ, এমন কুসংস্কারও প্রচলিত ছিল জনমনে।
খুব কম বয়সেই সাজেদা পাঠান বিরু’র বিয়ে হয়ে গেল শফীউজ্জামান খান এর সাথে। পাত্র বাড়ির পাশেরই আফতাব উদ্দীন খানের ছেলে। খান পরিবার তেমন স্বচ্ছল না হলেও বংশে খুব কুলিন। আফতাব উদ্দীনের মত তাঁর ছেলেও খুব ভদ্র। লেখা পড়া জানা। অত্যন্ত সুদর্শন।ছেলে মোহনগন্জে তার জাঁদরেল ডাক্তার মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে।সদ্য নতুন চাকুরীতে ঠুকেছে। আব্দুল হাই পাঠান কালবিলম্ব না করে তার মা হারা কনিষ্ঠা কন্যার জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে নিজেই খান বাড়িতে তসরিফ রাখলেন।
খান সাহেবের স্ত্রী সাহাতন নেসা।অবস্থাপন্ন বাপের বাড়ি, ডাক্তার ভাইয়ের আদরের ছোট বোন হবার সুবাদে প্রচন্ড জেদী এবং আত্মবিশ্বাসী নারী। নিরীহ খান সাহেবের তুলনায় সংসারে তিনিই উচ্চকণ্ঠ এবং প্রভাবশালী। স্বয়ং পাঠান সাহেব এবং গ্রামবাসী কারওই তা অজানা নয়।কিন্ত সাহাতন নেসা সানন্দে রাজি হলেন।
(৫)
বিয়ের পর সাজেদা পাঠান বিরু শশুড় বাড়ি এলেন। দীর্ঘদিন শশুড় বাড়ি অবস্থানের পর একসময় স্বামীর সাথে ঢাকাবাসী হয়ে শহরে এলেন।সংগে এলো পাঁচ দেবর-ননদ। তারা শহরে ভাইয়ের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করবে।সেই থেকে সীমিত আয়ের একটি সুবিশাল একান্নবর্তী পরিবার, শশুড়-শ্বাশুড়ি সহ নিজের সাত সন্তানের দেখভাল করতে করতেই জীবনের বড় একটি সময় কেটে যায় পাঠান কন্যার। একসময় সংসারের আয়তন ছোট হয়ে আসে। মফস্বলের ছোট্ট পরিসরে নিজের সন্তানদের নিয়ে একান্ত নিজস্ব সংসার গড়ে তোলেন তিনি। স্বামীর উপার্জন বাড়ার সাথে সাথে সংসারে স্বচ্ছলতাও আসে। ঢাকায় নিজের একাধিক বাড়ি, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা স্বামী, গৃহকর্মী, একাধিক সাহায্যকারী সবকিছু মিলিয়ে জীবন যখন ভরপুর, জমজমাট তখনই মাথার উপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। আকস্মিকভাবে, অকালে চলে গেলেন স্বামী শফীউজ্জামান খান।
কিন্তু তবুও জীবন থেমে থাকেনা। জীবন চলে জীবনের নিয়মে।বিরু’র চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রিয় দাদি ফরহাতন নেসার মুখখানা। প্রচন্ড সাহস, মনোবল নিয়ে তিনি লড়ে গেছেন তার সুদীর্ঘ জীবন। তিনিতো সেই ফরহাতন নেসা’রই উত্তরসূরি!
মা’য়ের দাদি সেই সাহসিকা ফরহাতন নেসা’র কোন স্মৃতি আমার মনে নেই। কিন্তু মা’র কাছে শুনলাম, তাঁকে আমি দেখেছি। তাঁর কোলে উঠেছি। তাঁকে আমি, আমার বড় বোন এবং কাজিনরা ডাকতাম, ‘পবন’ নামে। আজ সেই অজানা ‘পবন’ এর জন্য খুব মায়া হল। মনে হল, পবন তাঁর সাহসী জীবন দিয়ে আমাদের জন্য পথ দেখিয়ে গেছেন।
তাঁর পদচিণ্হ, তাঁর শরীরের ‘জিন’ হয়তো আমার অজান্তেই আমাকেও সাহসি হতে শেখায়। ‘না’কে না বলতে শেখায়!
“চিয়ার্স টু সাহসিকা পবন”!
লেখকঃ সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ইউএসএ প্রবাসী